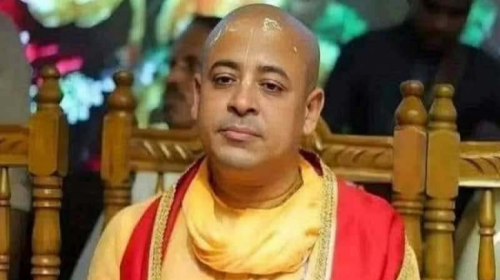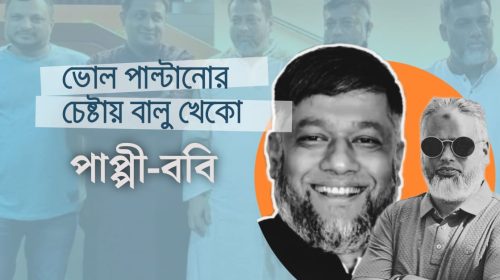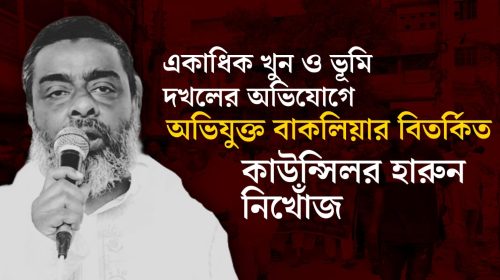বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ভাঙনের মিছিল শুরু হওয়া আসলে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; এটি ছিল পূর্বপরিকল্পনার অভাব, নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং আঞ্চলিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার একটি যৌক্তিক পরিণতি। শুরু থেকেই এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিজেদের একটি মনোপোলিস্টিক অবস্থানে রাখতে চেয়েছে, যেখানে আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে কেবল সমর্থনের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের কেন্দ্রীভূত চিন্তা-ভাবনা আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
চট্টগ্রামের মতো একটি অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং রাজনীতি মিশ্রিত হয়ে জনগণের পরিচয় তৈরি করেছে, সেই অঞ্চলকে কেন্দ্র থেকে অবজ্ঞা করার মানে ছিল একটি বিস্ফোরণকে আমন্ত্রণ জানানো। আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করত, তাহলে এমন ভাঙন নাও দেখা দিতে পারত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ জমে উঠেছে, কারণ তাদের অনুভূত হয়েছে যে, তাদের কেবল কর্মী হিসেবে দেখা হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হিসেবে নয়।
এই ভাঙন ফুকোর “পাওয়ার ডায়নামিক্স” তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমন একটি ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করেছিল, যা পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত এবং ঔপনিবেশিক মনোভাবের মতো কাজ করেছে। আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, এবং তাদের সিদ্ধান্তগুলো কেন্দ্রীয় নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতারা আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি।
তাছাড়া, ভাঙনের আরেকটি বড় কারণ ছিল আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই। ব্যক্তিগত ইগো এবং স্বার্থ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, তারা একটি যৌথ কাঠামো তৈরি করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। নেতৃত্বের এই বিচ্ছিন্নতাবোধ জনগণের ওপরও পড়েছে। একদিকে চট্টগ্রামের স্থানীয় নেতৃত্ব ক্ষোভে ফুঁসছে, অন্যদিকে সাধারণ ছাত্ররা আন্দোলনের আদর্শ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে।
এটি শেখ হাসিনার শাসনের প্রতিচ্ছবি মনে করিয়ে দেয়। শেখ হাসিনা যেভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করে নিজেকে অপরিহার্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও একই ভুল করেছে। ক্ষমতার মোহ তাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে, যেখানে তারা নিজেদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ভেবে নিয়েছে এবং আঞ্চলিক বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, কোনো আন্দোলন তার আঞ্চলিক ভিত্তি ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।
এই ভাঙন কেবল আন্দোলনের কাঠামোকেই নয়, এর নৈতিক ভিত্তিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। চট্টগ্রামসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এখন স্বাধীনভাবে নিজেদের পথ খোঁজার চেষ্টা করছে, যা শেষ পর্যন্ত একটি বৃহৎ ঐক্যকে চিরতরে ভেঙে দিতে পারে। এই প্রক্রিয়া যদি দ্রুত সমাধান করা না যায়, তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুধুই অতীতের একটি ব্যর্থ অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে।
নীচে দুইজন সাবেক সমন্বয়ক ও ২৪ এর আন্দোলনের সম্মুখ সারির যোদ্ধার গল্প দেওয়া হলো। এই দুইজনই নারী যোদ্ধা, যারা পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে শহীদদের সম্মানের তরে রাষ্ট্রের হাল ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্তর্কোন্দলের কারণে সম্ভব হয়ে উঠে নি।
সাবেক সমন্বয়ক নীলা আফরোজের গল্প (১৩ নভেম্বর ২০২৪):
“অভিমান করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিপ্লব নিয়ে আর কিছু লিখবো না। কিন্তু কিছু প্রশ্ন না করে পারছি না।
২৯ তারিখের ঘটনার কথা। সেদিনের মুভমেন্ট চলাকালীন ঘটনা সবাই জানে। কিন্তু নীরব চৌধুরীর একটা ফেক আইডি থেকে বলা হয়, আমার নাকি মহসিন কলেজের লীগ নেতা কাজী নাঈমের সাথে প্রেম ছিল। কোনো প্রমাণ ছাড়াই।
আমি ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে অনার্সে ভর্তি হই, আর ক্লাস শুরু করি জানুয়ারিতে। জানুয়ারির শেষে কাজী নাঈমের সাথে আমার ব্যাচের অদিতির বাকবিতণ্ডা হয়। অদিতির পক্ষ নেওয়ায় তার ক্রোধের মুখে পড়ি। এর পর থেকেই নানা ভাবে আমাকে ডিপার্টমেন্টের গ্রুপগুলোতে হেনস্থা করা হয়।
২০ থেকে ২৪—এই পাঁচ বছর ধরে আমি ছাত্রলীগ কর্তৃক নিপীড়িত।
২৯ তারিখের মুভমেন্ট থেকে ফেরার সময় চট্টগ্রাম কলেজের সহ-সমন্বয়ক লিজা উপস্থিত ছিলেন। হামলা হলে আমি তাকে এবং অন্যান্য মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে যাই। পরে এক ভাই আমাকে টেনে ভেতরে নেয়। মুহূর্মুহু গুলি চলছিল।
বাসায় ফেরার পথে জানতে পারি, বাড়িওয়ালা আমাকে আর রাখতে পারবেন না। লিজাও নিজের গৃহহীন অবস্থায় আমার সাথে কদিন ছিল। পরে আপুর বাসায় গিয়ে উঠি।
এবার আসি “ডট গ্যাং”-এর কথায়। এদের গুঞ্জন যেমন শুনেছি, তেমন কিছু প্রমাণও পেয়েছি। তবে আমি বিশ্বাস করি না, চবির সমন্বয়ক রিজাউর রহমান আর রাফি এ ধরনের কাজ করতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার।
“টোকাই নিধন কর্মসূচি” নামে একটা গ্রুপের স্ক্রিনশটও আমার কাছে আছে। যেখানে আমাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে।
কিন্তু এসব হয়েও কেন কেন্দ্র চুপ? কেন অভিযুক্তরা চুপ?
আমার আক্ষেপ এখানেই। যারা নির্দোষ, তারা চুপ কেন? প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবে কি?”
সাবেক সমন্বয়ক নাফিজা সুলতানা অমির গল্প (১৯ ডিসেম্বর ২০২৪)
“একটা সময় মনে হয়েছিল, আর কিছুই বলবো না। তবে এখন মনে হচ্ছে, কিছু বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। কেন আমি সরে এসেছি, সেই গল্পটা বলা জরুরি।
১৬ নভেম্বর ২০২৪, ঢাকায় চট্টগ্রামের সমন্বয়কদের ডেকে পাঠানো হয়। সেদিনই হাসনাত আব্দুল্লাহর সেই কথাটা প্রথম শুনি, “লিস্টেড সমন্বয়কদের আমরা ওউন করি। এর বাইরে কাউকে না।” এই কথাটা যে শুধু কথার কথা নয়, সেটা বুঝতে আর দেরি হয়নি। অভিযোগগুলো কেন্দ্রের সামনে তোলার পর তারা আশ্বাস দিয়েছিল, দুইটা তদন্ত কমিটি গঠন হবে। একটা নারী হেনস্থা, আরেকটা কিশোর গ্যাং নিয়ে।
কিন্তু এক মাস তিন দিন পেরিয়ে গেলেও কোনো পদক্ষেপ নেই। তাহলে কি ধরে নেবো এই দুইটা কমিটি গঠনে এক বছর লাগবে? নাকি এসব কথা বলা হয়েছিল শুধু পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য? হাসনাতের কথার মানে কি তাহলে সত্যি? নারী সমন্বয়কদের কি তারা ওউন করে?
চট্টগ্রামে ফিরে দেখলাম, এখানকার নারীদের এখনো কুরুচিকর মন্তব্য শুনতে হয়। কিশোর গ্যাংয়ের ছেলেরা এখনো প্রাধান্য পায়। অথচ কেন্দ্র কোনো জবাবদিহিতার ধার ধারে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হত্যা করা হলে দেশ উত্তাল হয়। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি মানুষ নয়? নাহিদ, আসিফ, হাসনাতের মতো প্রাইভেটের ছেলেদের হুমকি দেওয়া হলে “We are Nahid, Asif, Hasnat” লেখা হয় না।
কিন্তু চট্টগ্রামের সমন্বয়ক সিয়ামকে যখন মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বা সামীর উপর হামলা হয়, তখন কেন্দ্র চুপ থাকে কেন? তাহলে কি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওউন করে না?
আর খান তালাত মাহমুদ রাফির দুর্নীতির কথা তো ওপেন সিক্রেট। সবাই জানে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না। কেন্দ্রও চুপ। অথচ কেন্দ্র বলছে, “আমরা কিছু জানি না।” কিংবা হয়তো মনে করছে, “সব জেনেও চুপ থাকবো, কারণ আমরাও আওয়ামী লীগীয় ফ্যাসিস্ট চরিত্র ধারণ করেছি।”
তাহলে প্রশ্ন ওঠে, রাফির অভিযোগগুলো মিথ্যা হলেও কেন কেন্দ্র তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সুষ্ঠু তদন্ত করছে না?
আর তদন্ত কমিটি? সেটার কথা তো আর নাই বা বললাম। প্ল্যাটফর্ম যে নারীদের ওউন করতে পারে না, সেই প্ল্যাটফর্মকে আমি ওউন করি না। যে প্ল্যাটফর্ম কিশোর গ্যাং আর নারী হেনস্থাকারীদের জায়গা দেয়, সেই প্ল্যাটফর্মে আমি থাকতে পারি না।
সবাই দুর্নীতিতে যুক্ত নয়, এটা সত্যি। কিন্তু যারা এসব করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না কেন? এর ফলে পুরো প্ল্যাটফর্ম বিতর্কিত হচ্ছে। যাদের ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে কোনো পার্থক্য নেই, তাদের সাথেই থাকতে হবে আমাকে?
এই প্রশ্নগুলোই আমাকে বাধ্য করেছে সিদ্ধান্ত নিতে। আমি সরে গেছি।”
দুটি গল্পই রাজনৈতিক কাঠামোর একটি গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণের পথ দেখায়, যেখানে ক্ষমতা, আদর্শিক বিভাজন, এবং শোষণের রাজনীতি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে নেতৃত্বের ব্যর্থতা, কাঠামোগত দুর্বলতা, এবং ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতা সামাজিক আন্দোলন এবং ব্যক্তিগত জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে।
প্রথম গল্পটি মূলত একটি আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সংকটকে তুলে ধরে, যা “হেজিমনিক ক্রাইসিস” বা আধিপত্যের সংকটের দিকে ইঙ্গিত করে। এখানে নেতৃত্বের অবস্থান এক ধরনের “মোরাল অথরিটি” দাবি করে, কিন্তু তাদের কার্যক্রমে “ইনস্টিটিউশনাল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড” প্রকাশ পায়। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বললেও তারা কার্যত একটি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতেই আবদ্ধ থাকে, যেখানে নারীর নিরাপত্তা বা মতামতের গুরুত্ব তুচ্ছ করা হয়। এই ধরনের দ্বিচারিতা গ্রামশির “প্যাসিভ রেভ্যুলেশন” তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে পুরোনো শক্তি নতুন আঙ্গিকে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখে, কিন্তু প্রকৃত সংস্কারের পথে হাঁটে না।
এ গল্পে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যেও যে বৈষম্য রয়ে গেছে, তা রাজনৈতিক “স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স” এর উদাহরণ। নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠ রোধ করা এবং তাদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান না দেওয়া এই কাঠামোগত সহিংসতাকে আরও প্রকট করে তোলে। নারীর নিরাপত্তাহীনতা এবং নেতৃত্বের সাড়া না দেওয়া তাদের নৈতিক কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এতে বোঝা যায়, আন্দোলনটি আসলে “সিম্বলিক প্রোটেস্ট” এর চেয়েও বেশি কিছু হতে পারছে না, কারণ এর অভ্যন্তরীণ সংকট এবং নেতৃত্বের রাজনৈতিক উদাসীনতা।

দ্বিতীয় গল্পে আমরা দেখি, কিভাবে ব্যক্তি আক্রমণ এবং সামাজিক হয়রানির রাজনীতি বৃহত্তর আন্দোলনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে রাষ্ট্র ও সমাজের “মাইক্রো ফ্যাসিজম” কাজ করে। ফ্যাসিস্ট শক্তি এবং এর অনুগামী গোষ্ঠীগুলো তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে “চরিত্রহনন” কৌশল ব্যবহার করে। নারীদের লক্ষ্য করে সামাজিকভাবে হেয় করার এই কৌশল আসলে পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার হাতিয়ার, যা তাদের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে।
“ডট গ্যাং” এর মতো গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম ফুকোর “ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্যানিশ” তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে প্রতিপক্ষকে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে দমন করা হয়। এদের কাজ রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিজমের একটি “অর্গানিক এক্সটেনশন” হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিগত জীবনকে টার্গেট করে এবং ভয় দেখিয়ে এই গোষ্ঠীগুলো বৃহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলোকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের ঘটনা দেখায়, আন্দোলন কেবল বাহ্যিক প্রতিপক্ষ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং সামাজিক পিতৃতান্ত্রিকতার কারণে দুর্বল হয়।

দুটি গল্পেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পাশাপাশি সামাজিক কাঠামোর সংকটও উন্মোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে যে অবিশ্বাস এবং বিভক্তি তৈরি হয়, তা “স্ট্রাকচারাল ইনইকুইটি” বা কাঠামোগত বৈষম্যের একটি চিত্র। আন্দোলনের ভেতরকার বিভাজন রাষ্ট্রের “ডিভাইড অ্যান্ড রুল” কৌশলকে আরও কার্যকর করে তোলে। এই কৌশল সাধারণত রাষ্ট্র নিজে প্রয়োগ করে, তবে এখানে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকেও এই কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

এই দুটি গল্প সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক শোষণ, কাঠামোগত অবিচার এবং নেতৃত্বের অদক্ষতার প্রতীক। এগুলো দেখায়, কীভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার রাজনীতি এবং সামাজিক বৈষম্য একই মুদ্রার দুই পিঠ হয়ে কাজ করে। এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন তোলে—ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের দায়বদ্ধতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, এবং কীভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের লড়াই ফ্যাসিস্ট কাঠামোর বিরুদ্ধে কার্যকর হতে পারে।
এখন আসি আরেকজনের কথায়। না উনি পদত্যাগ করেন নি, তবে ত্যাগের সাথে সাথে সমন্বয়ক হিসেবে প্রচুর সুনাম ও সম্মানের দাবিদার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও জেলা সমন্বয়ক চৌধুরী সিয়াম এলাহী। কিন্তু তারও রয়েছে একই ধরনের অভিযোগ। তিনি সিটিজিপোস্টকে জানান, “দ্বিতীয় বারের মতো পায়ের উপর গাড়ি চাপা পড়লো তবে এইবার ভি আই পি -দের। তারপর ও বলে “তুমি এভাবে রিয়েক্ট করছো কেন?” এই ঘটনাটা কি হয়েছিল জানেন? বৈছাআ এর কেন্দ্রীয় নেতাদের গাড়ি আমার পায়ের উপর দিয়ে চাপা দিয়েছিল। পরিবেশ শান্ত রাখতে গাড়ির ভেতর থেকে একজন কেন্দ্রীয় নেতা সবাইকে শান্ত রাখার জন্য আমার নাম্বার নেয় এবং বলে যে উনি আমাকে ফোন দিবে। উক্ত ঘটনার পর প্রায় আমি ৩ সপ্তাহ ঠিক মতো হাটতে পারিনি। এক্স-রে রিপোর্ট এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আছে। সময় হোক, বলবো বিস্তারিত।”

তিনি আরো বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় জানি না আদৌও আর এই প্লার্টফর্মে আমি থাকবো কিনা। আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে যখন সবাই ক্রেডিটবাজি করছে তখন কিছু অপ্রকাশিত সত্য সবার সামনে আনতে চাই।
আমাদের কিছুজন যারা ১৫ই জুলাই থেকে ৩৬ জুলাই(৫ই আগষ্ট) পর্যন্ত সমন্বয়ক হয়েও সামনে এসে নেতৃত্ব দিতে সাহস করেনি তারাই ৫ই আগষ্ট পরবর্তী বৈছাআ এর বিভিন্ন কর্মসূচি তে সবার সামনে এসে এবং রাসেল-রাফি দুজনেরই পাশে দাঁড়িয়ে হয়ে গিয়েছেন মহা বিপ্লবী। অথচ, ১ জুন ২০২৪ – ১৪ জুলাই ২০২৪ কোটা আন্দোলন এবং ১৫ই জুলাই থেকে ৫ই আগষ্ট সরকার পতন আন্দোলন হয়।অর্থাৎ আন্দোলন ২ ভাগে বিভক্ত,১ম দিকের কোটা আন্দোলনে হামলার পর সরকার পতন আন্দোলনের দিকে যখন আমরা যাই তখন অনেকজন সম্মুখসারি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। মূলত বিপ্লবী তো তারাই যারা ১৫ই জুলাই থেকে ৫ই আগষ্ট পর্যন্ত চট্টগ্রামে আন্দোলনে ছিল এবং নেতৃত্ব দিয়েছে। অথচ,তারাই যারা ১৫জুলাই থেকে ৩৬ জুলাই পর্যন্ত গায়েব ছিল তারাই ৫ ই আগষ্ট পরবর্তী ফিরে এসে হয়ে গেলেন মহা নেতা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার পতন আন্দোলনে সরাসরি সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যদি রাসেল-রাফির পর নেতৃত্ব দিয়ে থাকে তবে সেটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের বর্তমান সেক্রেটারি আলী ভাই ( ১৭ই জুলাই, ২২ জুলাই, ৩১ জুলাই।)। এর বাইরে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ছিল। এখন যে মহান বিপ্লবী রা তারাই সবকিছু নেতৃত্ব দিয়েছে বলে চিল্লাচিল্লি করছে তারা সেই সময়ে খোঁজেই পাওয়া যেত না। না হলে চিন্তা করে দেখুন রাফি ৩ ই আগষ্ট লাইভে এসে রাসেল- রাফির পর সমাপ্তি ঘোষণা আমি করেছি বলে ভিডিও বার্তা দিল কেন? তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইয়েরা যারা এত লাফাচ্ছে তাদের নাম নিলো না কেন সেই সময়গুলোতে? কারণ, তখন তারা নেতৃত্ব দিলে তবেই তো। এখন কথা হচ্ছে ইদানীং যারা লাফালাফি করছে এদের মূল টার্গেট কমিটি তে পদ। কেউ আহ্বায়ক, কেউ সদস্য সচিব হতে চাই।অথচ যারা মূল আন্দোলনে রাসেল-রাফির পরে নেতৃত্ব দিতে আপনারা রাজপথে দেখেছেন তাদের কাউকেই দেখবেন না এসব পদ পদবির জন্য দৌড়াচ্ছে।
কেউ আহতদের ব্যবহার করছে তো কেউ নারীদের ব্যবহার করছে এভাবেই পদ নিশ্চিত করার জন্য ২/৩ বার যাবো না যাবো না করেও ঢাকা গেল পদ এর জন্য।
কথায় কথায় কেউ বীর চট্টলার নাম বেচে খাচ্ছে কেউ শহীদের রক্তের কথা বলে আবার কেউ জুলাই স্পিরিট। মূলত, সব গুলো উদ্দ্যেশ্য একটাই।”
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পালস বুঝতে ব্যর্থ হওয়া নিয়ে তীব্রভাবে সমালোচনা করা প্রয়োজন। তাদের কার্যক্রমে যে ঢালাও জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখা গেছে, তা চট্টগ্রামের মতো একটি সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় অঞ্চলের বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক অনুভূতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। এই অঞ্চলের আন্দোলনের ইতিহাস, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তারা যে ন্যূনতম সচেতন নয়, তা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চট্টগ্রামের মতো জায়গায় আন্দোলনের মূল ভিত্তি তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এই ব্যর্থতাই তাদের অতিরিক্ত জেদের আর অন্ধ ইগোর ফল।
চট্টগ্রাম এমন একটি শহর, যার রাজনৈতিক ইতিহাস কেবল বিদ্রোহের জন্যই বিখ্যাত নয়, বরং এটি একটি আঞ্চলিক গর্বেরও জায়গা। তবে এই গর্ব এবং ঐতিহ্যকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এক প্রকার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। তাদের কার্যক্রম প্রমাণ করে, তারা চট্টগ্রামের জনগণের সঙ্গে একটি সংযোগ তৈরি করতে পারেনি। এটি ফ্রানজ ফ্যাননের “ডিকলোনাইজেশন অব মাইন্ড” তত্ত্বকে মনে করিয়ে দেয়, যেখানে কেন্দ্রীয় আধিপত্য স্থানীয় সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়ন করে। তারা হয়তো ভুলে গেছে, আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু কখনও শুধুই একটি শহর বা অঞ্চল হতে পারে না—আন্দোলনের শক্তি আসে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সংহতিতেই।
তাদের জেদ আর ইগো এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেনো আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তারা নিজেদের রাজা মনে করছে। তারা ভুলে গেছে, রাষ্ট্র বা আন্দোলন কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এ বিষয়ে তারা হাসিনার কাছ থেকেই শিক্ষা নিতে পারে। শেখ হাসিনার শাসনব্যবস্থা দেখিয়েছে, কীভাবে ক্ষমতা এবং অহংকার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। হাসিনা রাষ্ট্রকে এমনভাবে চালিয়েছে, যেন এটি তার পারিবারিক ব্যবসা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও একই ভুল করছে—তারা আন্দোলনকে এমনভাবে দখল করে রেখেছে, যেন এটি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।
এই ক্ষমতার মোহ আর অহংকারের কারণেই তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, আন্দোলনের মূল শক্তি আসে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে। চট্টগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই নেতৃত্ব বুঝতে পারেনি, এখানকার মানুষ কেবল বড় বড় ভাষণ চায় না, তারা কাজ চায়, সংযোগ চায়। কেন্দ্রের এই দূরদর্শিতার অভাব দেখিয়ে দেয়, তারা আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরেও একটি “মাইক্রো-স্টেট” হিসেবে পরিচালনা করতে চেয়েছে, যেখানে স্থানীয়দের মতামত এবং অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র।
ক্ষমতার জন্য যে এই ধরনের জেদ আর অন্ধত্ব কেবল আন্দোলনই নয়, বরং সমগ্র নৈতিকতার ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়, তা তারা অনুধাবন করতে পারেনি। নেতৃত্বের এই অন্ধ অহংকার তাদের আরও একধাপ ফ্যাসিস্ট কাঠামোর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে তারা স্থানীয় বাস্তবতা আর জনগণের শক্তি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। চট্টগ্রামের জনগণের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতা কেবল আন্দোলন নয়, ভবিষ্যতে এই নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতাও চিরতরে ধ্বংস করতে পারে।